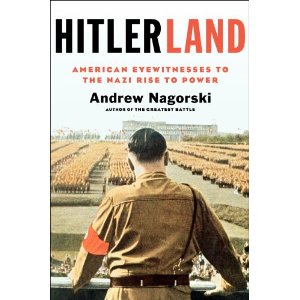সুজন সুপান্থ
মেঘসন্ধ্যার আকাশ
১.
তখন ঘন মঙ্গাআঁধার। খাঁ খাঁ উনুন। লাকরি আছে, হাড়ি আছে তবুও জ্বলেনি চুলা। জমি আছে, শস্য নেই। গোলাঘর আছে, চাল নেই। আমাদের মুখে মুখে হাসি আছে, আনন্দ নেই। আমরা সবাই পাশাপাশি ঘর, তবু দূরত্ব অসীম। মা আছে, মায়ের শাড়ির সেই ঘ্রাণটুকু আছে। শুধু শাড়ির আঁচলে বাঁধা আদর মাখানো কোনো খাবার নেই। এ রকম একটা ঘোর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অনেকটা দিন পেরিয়ে যেতে যেতে আমরা বড় হয়ে উঠি। একটু বড় হলেই কাউকে বলা বারণ, আজ দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি তেমন। বরং ঠোঁটে হালকা করে সরিষার তেল মেখে ঘুরে বেড়িয়েছি এ পাড়া ও পাড়া, কার্তিকদের বাড়ি। সবাই জেনেছিল, দুপুরে মোরগ-পোলাও খেয়ে ঠোঁটে তার চিহ্ন নিয়ে ঘুরছি। আর ভেবেছি—একদিন কার্তিকদের মতো শাকের অম্বল দিয়ে পেটপুরে ভাত খেয়ে কাঁইয়্যার বিলে রঙিন ঘুড়ি ওড়াতে যাবো।
২.
ঘুড়ি ওড়ানোর বাসনা দমিয়ে রোজ বিকেল বেলা পুকুর পাড়ে খেজুর গাছের আড়ালে নির্জনে বসে থাকলে বিনুদি কীভাবে যেন টের পেয়ে যেত। বিনু’দি পাড়াতেই থাকতো। স্কুল বন্ধু। তবু বিনু’দি আমার থেকে বড়, যতটুকু ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর দূরত্ব। সকাল বেলা টিফিনের টাকার জেদে স্কুল না যাওয়ার হুমকি দিলে, দূরত্ব পেরিয়ে এসে বিনুদি হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যেত। যেতে যেতে বলত, ‘কান্দিস না, মুই (আমি) তোক (তোমাকে) ঝালমুড়ি কিনি (কিনে) দিম (দেবো)।’ আর অমনি, বিনুদির হাত ঝুলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাথার ভেতর গুল জাফরের দোকানের ক্যাসেটে বেজে ওঠা গানের সুর ঢুকে যায়—হাওয়া মে উড়তা যায়ে, মোরা লাল দোপাট্টা মাল মাল।
তারপর ষষ্ঠ শ্রেনী ছুটি হয়ে গেলে নবম শ্রেণীর বেঞ্চে বিনু’দির পাশে চুপটি মেরে বসা। ঝালমুড়ি খেতে খেতে এক সময় বানানের সুরে বেঞ্চের ওপর খোদাই করা লেখা পড়ি—বিনু+সোম (সোমনাথ)। এই সুর কানে পৌঁছানো মাত্র মুখ চেপে ধরে কাছে টেনে নেয় বিনু’দি। তখন এই যোগ চিহ্নের মাজেজা বোঝা হয়নি অতটা। তবুও কেন যেন ইচ্ছে করত—নিজের নামের পরে যোগ চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখি ‘বিনু’দি’। ভাবতে ভাবতে ঘণ্টা বাজে। ছুটি হয় নবম শ্রেণী। বাড়ি ফিরি হাঁটতে হাঁটতে, বাড়ি ফেরে পার্শ্ববর্তীনি। প্যান্টের পকেটে মুঠো করে ধরে রাখি যোগ চিহ্নের খেয়াল।
তো যা বলছিলাম, পেটে খিদে নিয়ে বিকেলে পুকুর পাড়ে নির্জনে বসে থাকলে বিনু’দি ঠিক ঠিক ধরে ফেলত। বুঝতো খাওয়া হয়নি। ওর অবশ্য ঠোঁটে সরিষার তেল মাখতে হত না। এতে তাদের কোনো আক্ষেপ ছিল না কোনোদিন। কী খেয়েছিস আজ, এই প্রশ্নের উত্তর দিই, পানি। অমনি বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বিনু’দি। তারপর প্যান্টের কোচড় থেকে দুটো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পোড়া আলু বের করে বলে—আয় খাই। আমরা ক্ষুধা পেটে আলুপোড়া খাই; আর ঘুড়ির বদলে পুকুরের জলে উড়ে আসা বাতাসে দুটো ছায়ার পাশাপাশি এক হওয়া দেখি। ছায়া দুটো পুকুরের জলে ডুবে গেলে এক সাথে বাড়ি ফিরে আসি। এক সাথে ফিরি, তবু আমাদের বাড়ি, টিনের চাল, রাত্রিবেলার ঘর আলাদা সুরে বাজে। এই সুর নিয়ে অনেকটা রাত যেন মাতালের রাত। একবার এমন মাতাল রাতে ইকোনো কলমের খোঁচায় পর্দা সরিয়ে টেবিলের একদম মাঝে লিখে রাখি পুরনো খেয়াল—সোমনাথ নয়, আমার ডাকনামের পাশে বড় একটা যোগচিহ্ন তারপর বিনু’দির নাম। কলমের কালি পরে পরে সেই নাম কালো হয়ে যায়। চুপিচুপি রোজ এই দৃশ্য দেখে, কালো নাম ঢেকে রাখি হলুদ পর্দায়…
৩.
এত যে মঙ্গাআঁধার, তবুও বাড়ির সামনে ছিল সৌখিন ফুলের বাহার। পুরো বাগানজুড়ে শুধু বাবা-মায়ের পায়ের ছাপচিহ্ন। বাগানের প্রতিটি ফুল, ফুলে মধু নিতে আসা প্রতিটি প্রজাপতিও হয়তো বাবা-মাকে চিনে ফেলেছিল।
বাগানের প্রসঙ্গ এলে কেবলই বি নু দি র নামের বানান ভেসে ওঠে। সিঁদুর বিনু’দির খুব পছন্দ ছিল। বলতো, একদিন সিঁথিতে সিঁদুর মেখে বহুদূরে অন্য কোনো এক বাগানের দিকে চলে যাবে। সেখানে বিনুদি ফুলফুল খেলবে। আমি তাকে ‘না’ বলি। মন খারাপ করে থাকি, শব্দহীন। বিনু’দি কাতুকুতু দেয়, হাসি না। বাগান থেকে রক্তজবা তুলে বিনু’দির সিঁথিতে তার রঙ মেখে দিই। লাল হয়ে যায় সিঁথিপথ। এই লাল নিয়ে তাকে ধরে রাখতে চাই। বিনুদি খিলখিল হেসে ওঠে। তার হাসির শব্দ বুকের ভেতরে তীরের ফলার মতো এসে লাগে।
৪.
একদিন মেঘলা আকাশ। সেইদিন সন্ধ্যার আগে, পুকুর পাড়ে বাঁশপাতা দিয়ে নৌকা বানাতে বানাতে বিনু’দি বলেছিল, তুই কোথা থেকে এসেছিস জানিস নাকি! এদিকে মৌনস্বর, জানি না তো অতো। সেই সন্ধ্যায় বলেছিল—বাগান থেকে রে বোকা, বাগান থেকে। প্রজাপতির মতো সেই বাগানে ঢুকে কেউ ফুলফুল খেলে। জিতে গেলে খসে পড়ে ফুল। সেই ফুল অসীম আদরে বেড়ে বেড়ে আজ তুই এই ছটু। সেই বাগান দেখার বড় সাধ জাগে। সাধের পাশাপাশি আরও নাম না জানা কী যেন একটা জেগে ওঠে। আমার কেমন কেমন যেন লাগে। বাঁশপাতার নৌকা পুকুরে ছেড়ে দিয়ে কাশবনের দিকে যেতে যেতে বিনু’দি বাগান দেখাতে চায়। চঞ্চল হয়ে উঠি। হঠাৎ বিনু’দি পুকুরে লাফিয়ে ওপাড়ে চলে যায়। খিলখিল হাসতে হাসতে বলে, যদি সাঁতার দিয়ে কাছে যেতে পারি, তবেই ঘুরে আসা যাবে সেই বাগানের ঘ্রাণ। পারিনি। শুধু ঢেউয়ের তালে তালে বাঁশপাতা নৌকার চলে যাওয়া দেখেছি। তখনও সাঁতার শিখিনি আমি, এখন যেমন…অদেখাই থেকে গেল গোপন বাগান…
৫.
সেই রাতে বাড়ি ফিরে ভর করেছিল কী এক বিষণ্নতা! রাফখাতাজুড়ে কাটাকুটি আঁকি। আঁকি সেই মন খারাপের মেঘসন্ধ্যার আকাশ। অথচ আঁকতে গিয়ে প্রতিবারই মেঘলা আকাশটা কেন যেন বিনু’দির বুকের মতো গোল গোল হয়ে ওঠে। আমার অসহ্য লাগে। অভিমান জাগে।
৬.
এতকিছুর পরও বুকের ভেতর থেকে বিনু’দিকে দিই সকালের ফুল, বিকেল বেলার হাসি। রোজ দিই রক্তজবার সিঁদুর। তবু একদিন সকালবেলার বকুল ফুল হাতে নিয়ে শুনি বিনু’দি নেই। নেই মানে, সেই যে সোমনাথ, তার হাত ধরে ভোরের পাখির সুরে চলে গেছে অজানা বাগানের দিকে। বিনু’দি এখন ফুলফুল খেলে। আমার কান্না কান্না লাগে। এই সকালে আমারও কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হয় না…
৭.
বিনু’দির নাম মনে হলে এখন আমার ডানা খসে পড়ে। তার নাম মনে হলে, ভুল হয় নিজের নামের বানান। রাগে, জমানো অভিমানে কুটিকুটি করি কবিতার খাতা। এইসব হাহাকার নিয়ে সন্ধে্যবেলা ছুটি সুবর্ণদহের কাছে। সুবর্ণদহের জলের ঝাপটা এসে ছুঁয়ে ছঁুয়ে দেয় পা। ওপাড়ে আস্ত একটা মেঘ নেমে থাকে। আমি জলের ওপর ভাসিয়ে দিই বুকে জমা খিলখিল সুর। সেই সুর ভেসে ভেসে মেঘ ছুঁয়ে দিলে দহনপাড়ে বৃষ্টি নেমে আসে…এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে জেনেছি, নদীদেরও দহন আছে। তাদের আসলে আলাদা কোনো নাম নেই। সুবর্ণদহ, ঘাঘট কিংবা শ্যামাসুন্দরী, তারা জানে না তাদের নামের বানান। তারা সবাই ভিন্ন ভিন্ন দহন নিয়ে ছুটে চলা নদী।
৮.
এরপর কেটে গেছে অনেকটা বছর। কেটে গেছে মঙ্গাআঁধার কালো। বড় থেকে বড় হয়ে আছি, সুবর্ণদহ কিংবা শ্যামাসুন্দরী থেকে বহু বহুদূরে। এতটা দূরে এসে জেনেছি, আমারও একজন প্রেমিকা ছিল। অসীম নিঃসঙ্গতা নিয়ে ছিল। নিঃসঙ্গতার ভেতরে থাকতে থাকতে আরও কেউ তাকে ভালোবেসেছিল। সেও বেসেছিল। ভালো বাসতে বাসতে একদিন চোখের আড়ালে সে ফ্রিজশট হয়ে গেল।
৯.
এ পাড়ে বেজে উঠছে জলবালি-সোনারোদ সুর, ওপাড়ে আঁকা ঝুমঝুমপুর, রক্তজবার সারি, ওখানেই শিমলিদের বাড়ি। রোজ বিকেলে সে কাগজে ফুল বুনে বুনে নৌকার ভাষা। শ্যামাসুন্দরীর ঢেউটুকু পেরুলেই ভেসে ওঠে আহলাদপ্রবণ কথা। ঢেউয়ে ঢেউয়ে কথাদের ঘর। তারপর যে কথা উড়ে গেছে বহুদূর ঝুমুর হাওয়ায় ভেসে-তারাও জেনে গেছে, ঢেউয়ের গমকে কথা ভেসে দিয়ে কেউ কেউ ফেরতের ঢেউ গুণে চলে গেছে ঘর, সন্ধ্যার পর।
ও কথা, তুমি ভেসে যাও আজ, তোমার শব্দের কাছে আজ আর বসে নেই কোনা বিষণ্ন খেয়াল…